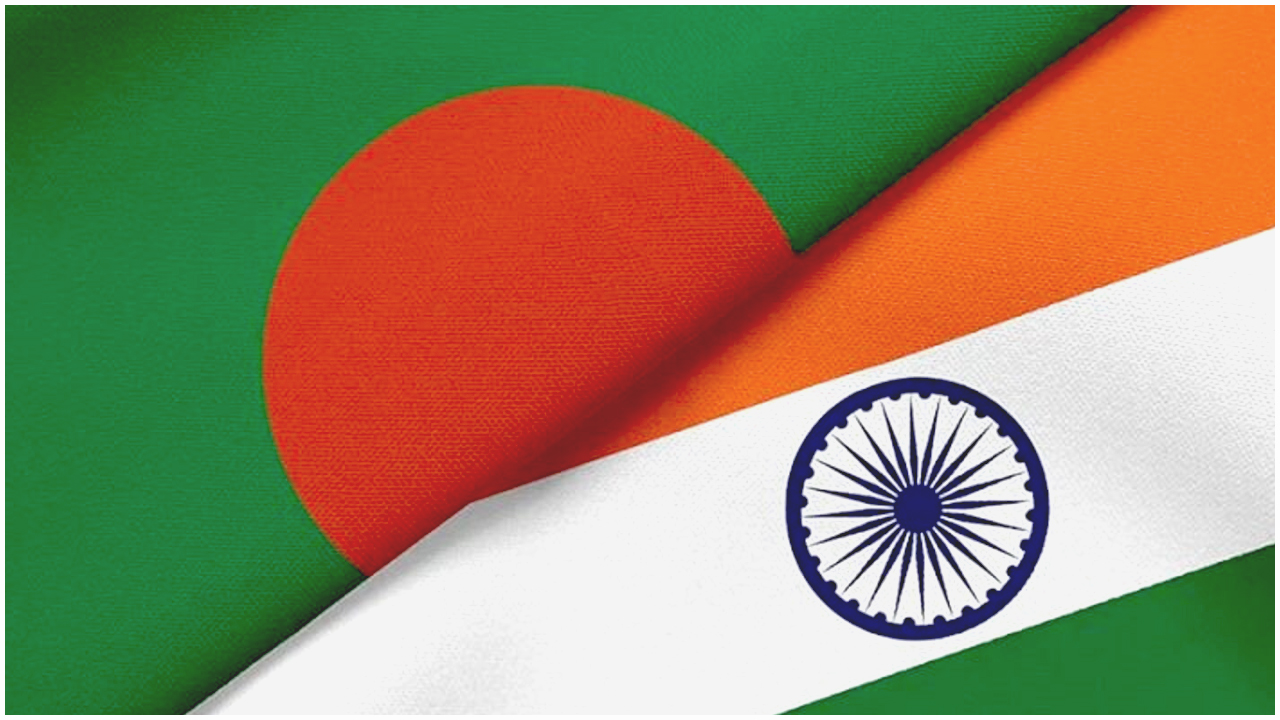গৌতমঘোষ,সরশুনা, বেহালা, কলকাতা, ভারত:
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় যে, ১৯৪৭সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ঘোষনার আগে থেকেই ব্রিটিশ শাসকগণ ভারত ভাগের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। তাদের একমাত্র লক্ষ ছিল কিভাবে ভারত বর্ষকে কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত করে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করে দেওয়া এবং সাথে চিরস্থায়ী অশান্তি ও হিংসাকে জিইয়ে রাখা। ভারত উপমহাদেশ কে ব্রিটিশ শাসকগণ চারটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত করেন। ভারত, পাকিস্থান, বার্মা বা বর্তমান মায়ানমার এবং সিংহল বা বর্তমানে শ্রীলঙ্কা এই চারটি রাষ্টে বিভক্ত করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনত ঘোষনা করেন। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ভারতবর্ষ আর মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্থান। নতুনগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্থান যা পশ্চিম-পাকিস্থান ও পূর্ব-পাকিস্থান মাঝে দুই হাজার কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত, ভারতবর্ষ।
পাকিস্থান সূষ্টির সময় পূর্ব-পকিস্থানের অর্থনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্থানের রাজধানী লাহোর হওয়াতে, প শ্চিম-পাকিস্থনে অধিক পরিমানে আর্থিক সংগতি সম্পন্ন ব্যবসায়ীর বাস ছিল। পূর্ব-পাকিস্থানে যা ছিল খুবই কম সংখক। ফলে সরকারি আর্থিক বরাদ্দের প্রভাব ছিল দুরকম। পূর্ব-পাকস্থানে দেশীয় ব্যবসায়ী গনের সংখ্যা খুব বেশি থাকার ফলে, শ্রমিক অস্থিরতা এবং উত্তেজনা পূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে পূর্ব-পাকিস্থানে বিদেশী বিনিয়োগ ছিল অত্যন্ত কম। ফল স্বরূপ পশ্চিম-পাকিস্থানের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শিল্পের দিকে অথচ পূর্ব-পাকিস্থানে নির্ভরতা ছিল কৃষিক্ষেত্রে। ফলে দুইখন্ডের অর্থনিতির ক্ষেত্রে একদমই সামঞ্জস্য ছিল না।
পাকিস্থান রাষ্ট্র – পাজ্ঞাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এবং পূর্ব-পাকিস্থান প্রদেশ নিয়ে। সবকটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রন ছিল পশ্চিম-পাকিস্থানের হাতে। ফলে সরকারি ভাবে তারাই অনেক বেশি পরিমানেআর্থিক সংস্থান ও সুবিধা ভোগ করতো। যদিও ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মোট রপ্তানির পরিমাণের ৭০ % এসেছে পূর্ব-পাকিস্থান থেকে। ধীরে ধীরে পশ্চিম-পাকিস্থানে বিপুল পরিমানে অর্থভান্ডার পূর্ব-পাকিস্থান থেকে স্থানান্তরিত করতে শুরু করেন। এইসময় কালে প্রায় ২৬ কোটি ডলার অর্থভান্ডার পূর্ব থেকে পশ্চিমে স্থানান্তরিত করেন। পূর্ব-পাকিস্থানের বাংলা ভাষি জনগন ছিল ৬০ থেকে ৭০ % বাকিরা ছিলেন ঊর্দু ভাষি। পাকিস্থানের সামরিক বাহিনীতেও ছিল বাংলা ভাষিরা সংখ্যালঘু। ১৯৬৪ সালে সামরিক বিভাগের সেনা বহিনীর বিভিন্ন শাখায় বাংলা ভাষি সৈনিক সংখা মাত্র ছিল ৬ %। এদের মধ্যে কেবল খুবই কম সংখক মাত্র কমান্ড পদে ছিলেন। যাদের মধ্যে কয়েকজন কারিগরী বিভাগের প্রশাসনিক পদে ছিলেন। তাছাড়া, বিশাল প্রতিরক্ষা ব্যয় সত্বেও পাকিস্থান সরকার যে কোনো চুক্তি, ক্রয় ও সামরিক সহায়তা এবং চাকুরির মতো সবরকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন পূর্ব-পাকিস্থানের জনগনকে ।
ভারতীয় উপ-মহাদেশের বঙ্গ জনপদের আদি ভাষাই ছিল বাংলা। যেটা রক্ষা করতেই পরবর্তীতে পূর্ব- পাকিস্থানের জনগন সংস্কৃতিক, ভৌগলিক, ভাষাগত পার্থক্য এবং রাজনৈতিক শোষন এবং নানা
বৈষম্যের কারণে আন্দলনের সুত্রপাত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানের প্রথম মুদ্রা, ডাকটিকিট, ট্রেনের টিকিট, পোস্টকার্ড ইত্যাদি থেকে বাংলাকে বাদ দিয়ে ঊর্দু ও ইংরেজি ভাষা
ব্যবহার করা হয়। পাকিস্থানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এই ঘোষণায় পর ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব-পাকিস্থানের পন্ডিত ও শিক্ষিত সমাজ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য নানাভাবে মতামত দিতে থাকেন। ওনারা দাবী করেণ যে ঊর্দু ভাষা রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ব-পাকিস্থানের শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে নিরক্ষর হয়ে পড়বেন। এছাড়া সব রকম সরকারি পদের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে যাবেন। ঠিক এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলা ভাষার সমর্থনে প্রথম “রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ” গঠন করা হয়। ১৯৪৮ র ফেব্রূয়ারী মাসে পাকিস্থানের গন-পরিষদের মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ইংরেজি ও ঊর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষায় বক্তিতা দেওয়া এবং সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। সমর্থন পান বেশ কয়েক জন সংসদ সদস্য গনের। পাকিস্থানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই প্রস্তাবকে পাকিস্থানের বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রচেষ্টা বলে বিবৃতি দেন। অনেক বিতর্কের পর সংশোধনটি ভোটে বাতিল করা হয়।
২৬ শে ফেব্রূয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং জগন্নাথ কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্দ্যোগে প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিং এ অংশগ্রহন করেন। তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় সইয়দ মহম্মদ আবজান এবং শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় আবদুল হামিদ দুজনকেই পদত্যাগ পত্রে সাক্ষর করতে বাধ্য করেন। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বন্দুক ও তোপের মুখে আন্দোলন চলতে থাকে। গ্রেফতার হন আন্দোলন রত অসংখ্য ছাত্র ও নেতাগন। যাদের মধ্যে ছিলেন মাননীয় মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, রফিকুল আলম, অলি সাহাদ, সৌকত আলি, কাজী নোলাম মাহামুদ, আফদুল লতিফ তালুকদার, সাহ মহম্মদ নাসির উদ্দিন, নরুল ইসলাম সহ আরও অনেকে। এর পর খাজা নাজিম উদ্দিন পরিষদের নেতা গনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুই পক্ষের মধ্যে আটটি বিষয়ে সমঝোতা হয়। যার মধ্যে অন্যতম ছিল, আন্দলনরত গ্রেফতার হওয়া সকল বন্দী ছাত্র ও নেত্রী বৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, পুলিশের অত্যাচারের জবাব দিহি করতে হবে, বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও রাষ্ট্রভাষার
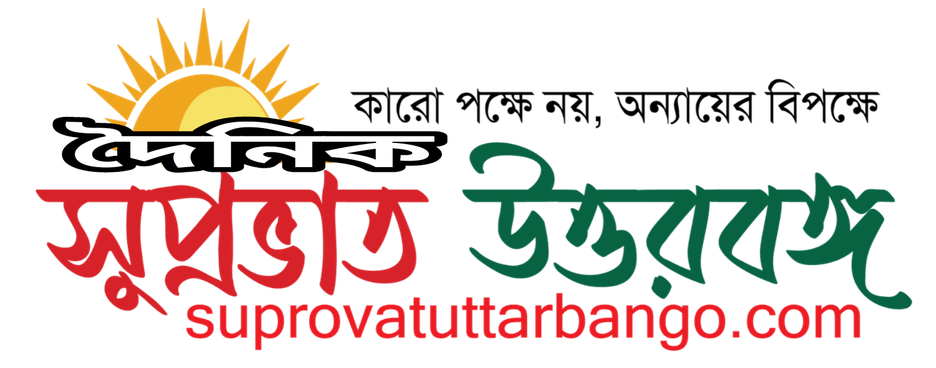
 Reporter Name
Reporter Name